স্মৃতির দখিন দুয়ার : লিখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- Update Time : বুধবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৩
- ১৯৪ Time View

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামখানি একসময় মধুমতি নদীর তীরে ছিলো। বর্তমানে মধুমতি বেশ দূরে সরে গেছে। তারই শাখা হিসেবে পরিচিত বাইগার নদী এখন টুঙ্গিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে কূল কূল ছন্দে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। রোদ ছড়ালে বা জ্যোৎস্না ঝরলে সে নদীর পানি রূপোর মতো ঝিকমিক করে।
নদীর পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান-পাট-আখ ক্ষেত, সারিসারি খেজুর, তাল-নারকেল-আমলকি গাছ, বাঁশ-কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতা-পাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসের চিকন লম্বা লম্বা সতেজ ডগা। শালিক-চড়ুই পাখিদের কল-কাকলী, ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘুর ডাক। সব মিলিয়ে ভীষণ রকম ভালোলাগার, একটুকরো ছবি যেন।
আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে এই টুঙ্গিপাড়া গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্যদিয়ে আমি বড়ো হয়ে উঠি।
আমাদের বসতি প্রায় দুশো বছরের বেশি হবে। সিপাহী বিপ্লবের আগে তৈরি করা দালান-কোঠা এখনো রয়েছে। আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা সেখানে বসবাস করেন। তবে বেশিরভাগ ভেঙে পড়েছে, সেখানে এখন সাপের আখড়া। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক গোলমাল হতো। মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গেও গন্ডগোল লেগেই থাকত। একবার এক মামলায় এক ইংরেজ সাহেবকে হারিয়ে জরিমানা পর্যন্ত করা হয়েছিল। ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে সেই ভাঙা দালান এখনো বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনাবাহিনী ঐ দালানের ওপর হামলা চালিয়েছিল। আমার দাদা-দাদিকে সামনের রাস্তায় বসিয়ে রেখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল।
আমাদের গ্রামে ঢাকা স্টিমারে যেতে সময় লাগত সতেরো ঘণ্টা। রাস্তাঘাট ছিলই না।
নৌকা ও পায়ে হাঁটা পথ একমাত্র ভরসা ছিল। তারপরও সেই গ্রাম আমার কাছে বিরাট আকর্ষণীয় ছিল। এখন অবশ্য গাড়িতে যাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পিডবোটেও যাওয়া যায়। গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া নৌকায় যেতে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে।
আমার শৈশবের স্বপ্নরঙিন দিনগুলো কেটেছে গ্রাম-বাংলার নরম পলিমাটিতে, বর্ষার কাদা-পানিতে, শীতের মিষ্টি রোদ্দুরে, ঘাসফুল আর পাতায় পাতায়। শিশিরের ঘ্রাণ নিয়ে, জোনাক-জ্বলা অন্ধকারে ঝিঁঝির ডাক শুনে, তাল-তমালের ঝোপে বৈঁচি, দিঘির শাপলা আর শিউলি-বকুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে, ধূলোমাটি মেখে, বর্ষায় ভিজে খেলা করে। আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি করতেন। বেশিরভাগ সময় তাঁকে তখন জেলে আটকে রাখা হতো। আমি ও আমার ছোটভাই কামাল মায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে দাদা-দাদির কাছে থাকতাম। আমার জন্মের সময় বাবা কলকাতায় পড়তেন, রাজনীতি করতেন। খবর পেয়েও দেখতে আসেন বেশ পরে।
আমার বাবা যখনই সময় ও সুযোগ পেতেন একবার বাড়ি এলে আমরা কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে নড়তাম না। বাবার কোলে বসে গল্প শোনা, তার সঙ্গে খাওয়া, আমার শৈশবে যতটুকু পেয়েছি তা মনে হতো অনেকখানি।
বাবাকে একবার গোপালগঞ্জ থানায় আনা হলে দাদার সঙ্গে আমি ও কামাল দেখতে যাই। কামালের তো জন্মই হয়েছে বাবা যখন ঢাকায় জেলে। ও বাবাকে খুব কাছ থেকে তখনো দেখেনি। আমার কাছেই বাবার গল্প শুনত মুগ্ধ হয়ে। গোপালগঞ্জ জেলখানার কাছে পুকুর পাড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বাবাকে নিয়ে যাবে কোর্টে তখনই আমরা দেখব। কামাল কাছ ঘেঁষে বলল : হাচুপা, তোমার আববাকে আববা বলতে দেবে।
আমার শৈশবের হৃদয়ের গভীরে কামালের এই অনুভূতিটুকু আজও অম্লান হয়ে আছে।
বাবাকে আমাদের শৈশবে-কৈশোরে খুব কমই কাছে পেয়েছি। শৈশবে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত ছিলাম বলে দাদা-দাদি, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের মানুষের অশেষ স্নেহ-মমতা পেয়েছি।
আমাদের পরিবারের জন্য মৌলবি, পন্ডিত ও মাস্টার বাড়িতেই থাকতেন। আমরা বাড়ির সব ছেলেমেয়ে সকাল-সন্ধা তাঁদের কাছে লেখাপড়া শিখতাম। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলেও কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলাম। আমার কৈশোরকাল থেকে শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ১৯৫২ সালে আমার দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ির নিজস্ব নৌকায় চড়ে প্রথম ঢাকা শহরে আসি। আমার স্নেহময়ী দাদা-দাদি ও আত্মীয়-স্বজন বেশিরভাগ গ্রামে বস করতেন। স্কুলে ছুটি হলে বা অন্যান্য উৎসবে বছরে প্রায় তিন-চারবার গ্রামে চলে যেতাম। আজও আমার গ্রামের প্রকৃতি, শেশব আমাকে ভীষণভাবে পিছুটানে।
আমার শৈশবের দিনগুলো ভীষণ রকম স্মৃতিময়। আজ সেসব দিনের কথা যেন স্মৃতির দখিন দুয়ার খোলা পেয়ে বারবার ভেসে আসছে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমার বাবার এক চাচাতো বোন, আমার চেয়ে বয়সে তিন-চার বছর বড়ো হবে। সেই ফুফুর সঙ্গে বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছি। খালের ওপর ছিল বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে হবে। প্রথমদিন কি দারুণ ভয়ে পেয়েছিলাম।
আমার হাত-পা কাঁপছিলো। ফুফুই আমাকে সাহস দিয়ে হাত ধরে সাঁকো পার করিয়ে দিয়েছিল। এরপর আর কখনও ভয় করেনি। বরং সবার আগে আমিই থাকতাম।
খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে পা ভিজানো আমার কাছে ভীষণ রকম লোভনীয় ছিল। নদীর পানিতে জোড়া নারকেল ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে টেংরা-পুটি-খল্লা মাছ ধরা। বর্ষাকালে খালে অনেক কচুরিপানা ভেসে আসত। সেই কচুরিপানা টেনে তুললে তার শেখড় থেকে বেড়িয়ে আসত ‘কৈ ও বাইন’ মাছ। একবার একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।
বৈশাখে কাঁচা আমর পেড়ে কুচি কুচি করে কেটে সর্ষে বাঁটা ও কাঁচা মরিচ মাখিয়ে, তারপর কলাপাতা কোনাকুনি করে সেই আম মাখা পুরে, তার রস টেনে খাওয়ার মজা ও স্বাদ আমাকে এখনো আপ্লুত করে রাখে। কলাপাতায় এই আম মাখা পুরো যে না খেয়েছে, সে কিছুতেই এরর স্বাদ বুঝবে না। আর কলাপাতায় এ আম মাখা পুরলে তার ঘ্রাণই হতো অন্যরকম। এভাবে আম খাওয়া নিয়ে কত মারামারি করেছি। ডাল ঝাঁকিয়ে বরুই পেড়ে কাড়াকাড়ি করে খেতাম। গ্রামের বড়ো তালাবের (পুকুর) পাড়ে ছিল বিরাট এক বরুই গাছ। ঝাঁকুনির ফলে লালের আভা লাগা সব থেকে টলটলে বরুইটা পুকুরের গভীর পানিতে গিয়ে পড়ত এবং কারো পক্ষে কিছুতেই সেটা যখন তুলে আনা সম্ভব হতো না তখন সেই বরুইটার জন্য মন জুড়ে থাকা দুঃখটুকু এখনো ভুলতে পারলাম কই?
পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমার দাদার একটি বড়ো নৌকা ছিল, যার ভেতরে দুটো ঘর ছিল, জানালাও ছিল বড়ো বড়ো।
নৌকার পেছনে হাল, সামনে দুই দাঁড় ছিল। নৌকার জানালায় বসে নীল আকাশ আর দূরের ঘন সবুজ গাছপালা ঘেরা গ্রাম দেখতে আমার বড়ো ভালো লাগত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই নৌকা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। শৈশবের ফেলে আসা সেই গ্রাম আমার কাছে এখনো যেন সুভাসিত ছবির মতো।
আমার বাবার জন্মস্থানও টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি এখন ঐ গ্রামের মাটিতেই ছায়াশীতল পরিবেশে ঘুমিয়ে আছেন। তার পাশেই আমার দাদা-দাদির কবর। যারা আমার জীবনকে অফুরন্ত স্নেহ-মমতা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন, আজ আমার গ্রামের মাটিতেই তারা মিশে আছে। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে আমার মা, বাবা, ভাই ও আত্মীয়-স্বজন অনেককে হারাই। দেশ ও জাতি হারায় তাদের বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা, আশা-আকাংক্ষার স্বাধীন সত্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।
ঘাতকের দল বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা থেকে সরিয়ে সেই মহাপুরুষকে নিভৃতে পল্লির মাটিতেই কবর দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে- কিন্তু পেরেছে কি?
বাবার কাছাকাছি বেশি সময় কাটাতাম। তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আলোচনা করার সুযোগও পেতাম। তাঁর একটা কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই বলতেন- ‘শেষ জীবনে আমি গ্রামে থাকব। তুই আমাকে দেখবি। আমি তোর কাছেই থাকব’। কথাগুলো আমার কানে এখনো বাজে। গ্রামের নিঝুম পরিবেশে বাবার মাজারের এই পিছুটান আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বারবার আমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।
আমি এখন নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছি। দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমার জীবনের শেষ দিনগুলো আমি টুঙ্গিপাড়ায় স্থায়ীভাবে কাটাতে চাই। খুব ইচ্ছে আছে নদীর ধারে একটা ঘর তৈরি করার।
আমার বাবা-মার কথা স্মৃতিকথামূলকভাবে লেখার ইচ্ছে আছে। আমার বাবা রাজনীতিবিদ মুজিবকে সবাই জানতেন। কিন্তু ব্যক্তি মুজিব যে কত বিরাট হৃদয়ের ছিলেন, সেসব কথা আমি লিখতে চাই।
গ্রামকে তো আমি আমার শৈশবের গ্রামের মতো করেই ফিরে পেতে চাই। কিন্তু চাইলেই তো আর হবে না। এখন সময় দ্রুত বদলাচ্ছে। যান্ত্রিকতার স্পর্শে গ্রামের সরল সাধারণ জীবনেও ব্যস্ততা বেড়েছে, চমক জেগেছে। মানুষও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।
এই শতাব্দীতে বাস করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর গ্রামীণ জীবনের মানোন্নয়ন ও শ্রমের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে।
আমার শত ব্যস্ততা থাকলেও এবং একটু সময় পেলেই আমি চলে যাই। কেন যে মনে হয় আমার শৈশবের গ্রামকে যদি ফিরে পেতাম। গ্রামের মেঠোপথটা যখন দূরে কোথাও হারিয়ে যায় আমার গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে করে, ‘গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে…’’।
শৈশব ও কৈশোরের স্কুল পাঠ্য বইয়ের গ্রাম সম্পর্কিত কবিতাগুলো আমার খুব সহজেই মুখস্থ হয়ে যেত। ‘আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর’, ‘তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়ে’, ‘বহুদিন পরে মনে পড়ে আজ পল্লি মায়ের কোল’, ‘বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ’, ‘মঘেনা পাড়ের ছেলে আমি’, ‘ছিপখান তিন দাঁড়, তিনজন মাল্লা’, তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে’- এসব কবিতার লাইন এখনো মনে আছে।
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণদ্বারে পাঠিকা হিসেবে যখন আমি প্রবেশ করি, তখন তো আমি কিশোরী। পরে হয়েছিলাম ছাত্রী। গ্রামভিত্তিক উপন্যাস, গল্প ও কবিতা যখনই সুযোগ পেয়েছি পড়েছি। বিভূতিভুষণের ‘পথের পাঁচালী’ আমাকে প্রথম ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে। এখনো হাতের কাছে পেলে পাতা উল্টাই। দুর্গা ও অপু দু’ভাইবোনের ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, খুনসুটি, গ্রামময় ঘুরে বেড়ানো, কিছু পেলে ভাগাভাগি করে খাওয়া, অপুর প্রতি দুর্গার কর্তব্যবোধ, দুর্গার অসুখ ও মৃত্যু। অপুর দুঃখ ও দিদিকে হারানোর বেদনা বুড়ি ঠাকুরমার অভিমান, দুঃখ-ব্যথা, অসহায়ত্ব। অপুর মা সর্বজয়া, দুঃখ-দারিদ্র্য যার নিত্যসঙ্গী, জীবনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যার সংগ্রাম, সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা। অপু-দুর্গার বাবার প্রবাস চাকরি জীবন, দুর্গার মৃত্যুর পর তারজন্য বাবার আনা শাড়ি, এসব ছোট্ট ছোট্ট দুঃখময় বাস্তব জীবনের বহু খন্ড খন্ড চিত্র তো বাংলাদেশের গ্রাম জুড়ে আজও রয়েছে। পথের পাঁচালী আমার নিজের গ্রামকেই মনে করিয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে পথের পাঁচালী শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পগুলোও আমার ভীষণ প্রিয়। গ্রামকে নিয়ে শিল্পী জয়নুল আবেদীনের স্কেচগুলোও বাস্তব। কলাগাছের ঝোপে নোলক পরা বউয়ের ছবিটি এখনো মনে পড়ে।
আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও মোটেই অনুল্লেখ করার মতো নয়। বাউল গান, বৈষ্ণব গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী মাঝির গান এসবই আবহমান কালের গৌরব।
গ্রামই আমাদের জীবন। আলোকোজ্জ্বল আধুনিকা রাজধানী ও শহরকে বাঁচিয়ে রাখছে গ্রামীণ অর্থনীতি আর মানুষ। ছোট-বড়ো সব গ্রামকেই আমাদের ঐতিহ্য অনুসারী আধুনিক ও আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
গ্রামোন্নয়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক সরঞ্জামসহ হাসপাতাল, স্কুল, মাতৃসদন, কৃষি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খেলার মাঠ প্রভৃতি থাকবে। ঘরবাড়ির অবস্থা মজবুত ও পরিচ্ছন্ন হবে। রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও পাকা হবে, যানবাহন চলাচলে সুব্যবস্থা করে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর করে তুলতে হবে।
কৃষিজমিগুলো সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত করে কৃষিব্যবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বন্টনসহ উৎপাদিত শস্য যাতে নির্ধারিত মূল্যে বাজারজাত করা হয় ও খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যসম্মত হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রাম থেকে উৎপাদিত খাদ্যশস্য সহজপ্রাপ্য করে তুলতে হবে। যেসব উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী রফতানি হবে ও কাঁচামাল হিসেবে কারখানায় যাতে তার সুষ্ঠু সরবরাহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। কৃষিকাজকে আধুনিকীকরণ করে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। সারাবছর ধরে মৌসুমানুযায়ী সকল প্রকার ফসল দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ উৎপাদন করতে হবে। কোনো জমি পতিত পড়ে থাকবে না। নদ-নদী, খাল-বিল, দিঘি-পুকুরে মৎস্য চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। গবাগিপশু ও হাঁস-মুরগির ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য রেখে খামার গড়ে তুলতে হবে। সারা বিশ্বে আজ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন হচ্ছে। আমাদের এই দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিখার দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় জমাবে না। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ও কৃষি উপকরণ সহজ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে সারাবছর কর্মব্যস্ত রাখতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারী গ্রামীণ কুটির শিল্পের মানোন্নয়ন করে ব্যপক প্রসার ঘটাতে হবে। গ্রামীণ কৃষিজাত পণ্য ও ছোট-বড়ো সকল ব্যবসআ এবং শিল্প বিকাশের পথ করে দিতে হবে। এর ফলে কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। আমি মনে করি আধুনিক বা যুগোপযোগী কৃষিব্যবস্থাই আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। এইসঙ্গে যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত হয়ে আসা অবহেলিত কৃষকদের পোড়াখাওয়া দুর্ভিক্ষ-দারিদ্যেক্লিষ্ট ভাগ্যকেও পরিবর্তিত করে তার বেঁচে থাকার ন্যুনতম অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করতে হবে।
আমাদের গ্রামের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি পশ্চাৎপদ। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক বিধিনিষেধ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বেড়াজাল ভেঙে তাদের মেধা বিকাশের পথ করে দিতে হবে। তাদের শ্রমশক্তিকেও সমমর্যাদায় উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে তারা নানারমক অনাচার-অবিচারের শিকার হয়ে থাকে। মেয়েরা সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ পেলে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়ালে মননে-ব্যক্তিত্বে সাহসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেলে কোনো প্রকার নির্যাতন বা শোষণ তাদের অন্তরায় হয়ে থাকবে না। নিজের অধিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মেয়েদেরই শক্ত হাতে নিতে হবে। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে হবে।
গ্রামের উন্নতিকল্পে আরো একটি বিষয় আমাকে ভীষণ রকম আতঙ্কিত করে তোলে।
সেটা হলো, আমাদের সবচেয়ে অবহেলিত অসহায় অংশ পুষ্টিহীন কঙ্কালসার শিশুর সংখ্যাধিক্য। দেশের সর্বত্র আমি যে গ্রামেই গিয়েছি এই একই চেহারার শিশুদের দেখেছি। এসব শিশু যখন জন্ম নিচ্ছে, তখন অবশ্যই তাদের ভবিষ্যতকে সম্ভাবনাময় ও নিরাপত্তাপূর্ণ করে তুলতে হবে। তাদের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকে আনন্দময় ও সুখময় করে তোলার এ উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে। তাদের সচ্ছল-সমৃদ্ধময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেও আমাদের বর্তমানকে তাদের জন্য উৎসর্গ করার দৃঢ় মানসিকতা গ্রহণ করা উচিত। এবং সেই সঙ্গে সকলকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে সক্ষম জনগণকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাতে হবে।
গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলতে আমি কোনো ছিঁটেফোঁটা বা সাময়িক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নই। যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে পড়ে থাকা পশ্চাৎপদ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত প্রাচীন কৃষিব্যবস্থার প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সামগ্রিক সংস্কার করে আধুনিক গ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আমি কোনো অনুদানমূলক বা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উন্নয়ন নয়, ‘টোটাল’ বা ‘সামগ্রিক’ উন্নয়ন চাই। এজন্য প্রয়োজনবোধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষিত সচেতন তরুণ সমাজকে কাজে নামাতে হবে।
গ্রাম-জীবনের অসংখ্য চরিত্র আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমাদের গ্রামের আক্কেলের মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। বুড়ী হয়ে গেছে এখন। তিন ছেলে তার। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলো। গ্রামের সব পাড়ায়, ঘরে ঘরে তার অবাধ যাতায়াত। সব ঘরের হাঁড়ির খবর তার নখদর্পণে। সে যেন গ্রামের গেজেট। কার ঘরে রান্না করতে হবে, পিঠে বানাতে হবে- সব কাজে আক্কেলের মা হাজির। আমরা যখনই গ্রামে যাই পিঠা তৈরি বা তালের ফুলুরি বানাতে তার ডাক পড়তো। পথে যেতে তার ঘরে একবার ঢুঁ মারলে পিঁড়ি পেতে বসাবেই, পান-সুপারিও খাওয়াবে।
ধান কাটার মৌসুমে দক্ষিণ দিক থেকে অনেক লোক আসত। ‘পরবাসী’ নামে তারা পরিচিত। ধান কাটা, মাড়াই প্রভৃতি কাজ তারা করত। ছোট্ট খুপরি ঘর তুলে পুরো মৌসুমটা থাকত। ধান তোলা হলে নিজ নিজ অংশ নিয়ে তারা চলে যেত। বর্ষার মৌসুমে নৌকায় করে বেদেনীরা আসতো। রং-বেরঙের কাঁচের চুড়ি আমাদের হাত টিপে-টিপে পরিয়ে দিত। ফিতে, আলতা, চিরুণি, আয়না, নানা ধরনের খেলনা ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বছরের নির্ধারিত সময়টাতে তারা ঠিক সময়মতো চলে আসত। আবার কখনো সাপের খেলা দেখাতো, বাঁশি বাজিয়ে কতরকম গান শোনাত। গ্রামের বৌ-ঝিরা তাদের কাছে ভিড় জমিয়ে দেশি টোটকা ওষুধ নিত। ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি কত প্রকার তাবিজ তারা দিয়ে যেত সবাইকে। বিনিময়ে ধান-চাল-খুদ বা সবজি-ডিম-মুরগিও নিত।
গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে ক্ষেত-খামারে এ ধরনের অসংখ্য বিচিত্র জীবনের চরিত্র রয়েছে। দু’মুঠো অন্নের আকাঙ্ক্ষায় যে কৃষক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, চৈত্রের রোদে পুড়ে রুক্ষ ক্ষেতে লাঙ্গল টানে, বর্ষায় বুক-সমান পানিতে ডুব দিয়ে পাট কাটে, শীতের প্রচন্ড কাঁপুনি সহ্য করে ফসল কাটে- তার জীবনসংগ্রাম কি অন্য যে কোনো সংগ্রামের চেয়ে কম মূল্যবান?
আমি জানি আমার গ্রামের সেই সুন্দর দিনগুলো আর কখনো ফিরে আসবে না। একে একে সব হারিয়ে গেছে। আমার সেই চিরচেনা গ্রাম, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত সেই মানুষগুলোও নেই। নেই মানুষের সেই মন-জীবন। যুদ্ধে সবাই যেন আজ পরাজিত। সেই কোমল সত্তারও মৃত্যু ঘটেছে। আজ শুধু বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা। আর তাই বেড়েছে স্বার্থপরতা, সংঘাত। হারিয়ে গেছে ভ্রাতৃত্ববোধ, সংকুচিত হয়েছে প্রসারিত হাত। জানি না এর শেষ কোথায়।
আমার জন্ম হয়েছে গ্রামে, শৈশবের রঙিন দিনগুলো উপভোগ করেছি গ্রামে। গ্রামীণ স্বভাব, চালচলন, জীবনযাত্রা ও মানসিকতার সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক। এখনো একটু সময় ও সুযোগ পেলেই আমি হাঁপিয়ে উঠি বলেই গ্রামে চলে যাই। শহরের যান্ত্রিক ব্যস্ততম জীবন থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামের নিরিবিলি নিঝুম শান্ত প্রকৃতিতে গেলে আমার দুচোখে শান্তির ঘুম নেমে আসে। রাজধানীতে এমন ঘুম পাওয়া কষ্টকর। এখানে বাতাস খুব ভারি, শ্বাস নিতেই তো কষ্ট। রাতের তারাভরা খোলা আকাশ অনেক বড়ো সেখানে।
নিম, কদম, তাল-নারিকেল গাছের পাতা ছুঁয়ে, ছন্দময় শব্দ তুলে ছুটে আসে মুক্ত বাতাস। জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’ যেন আমার গ্রাম-ঘন সবুজ প্রাকৃতি ও ফসলের প্রান্তর দেখে দুচোখ জুড়িয়ে যায়। নির্জন দুপুরে ভেসে আসে ঘুঘু আর ডাহুকের ডাক, মাছরাঙ্গা টুপ করে ডুব দিয়ে নদী থেকে ঠিকই তুলে আনতে পারে মাছ। এরচেয়ে আর কোনো আকর্ষণ, মোহ, তৃপ্তি আর কোনো কিছুতেই নেই আমার। ধুলি-ধুসরিত গ্রামের জীবন আমার আজন্মের ভালোবাসা। আমার হৃদয়ের গভীরতম অনুভুতি।
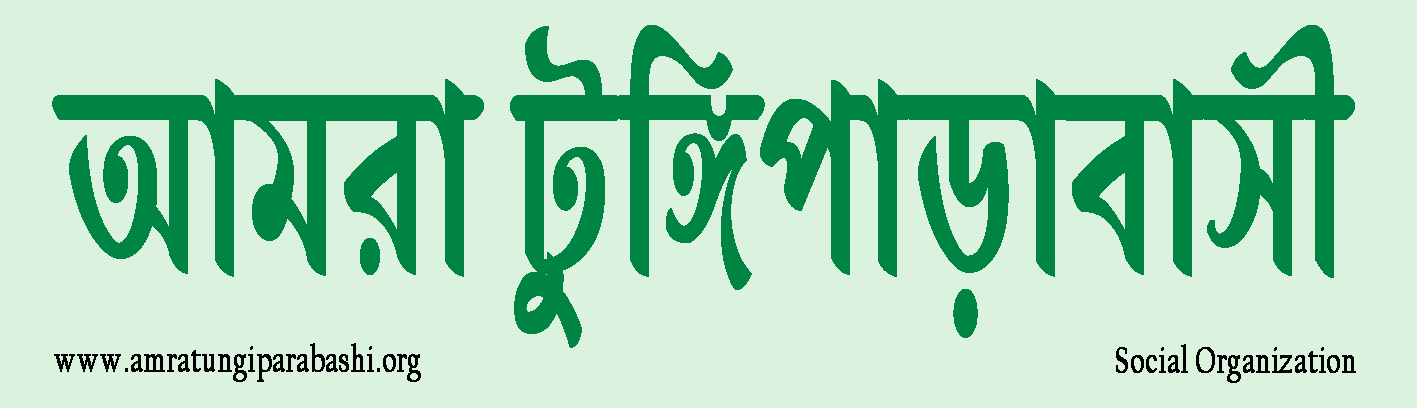






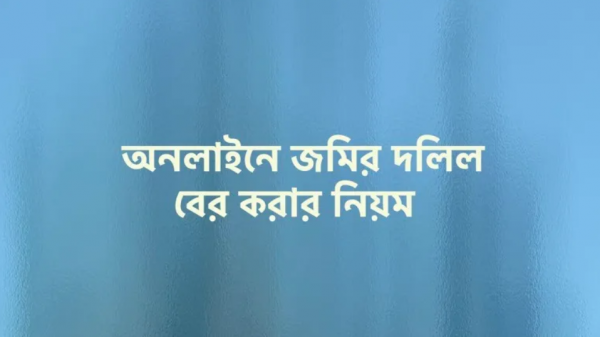





Leave a Reply